অব্যক্ত
| ৯ চৈত্র ১৪১৯ | Saturday, March 23, 2013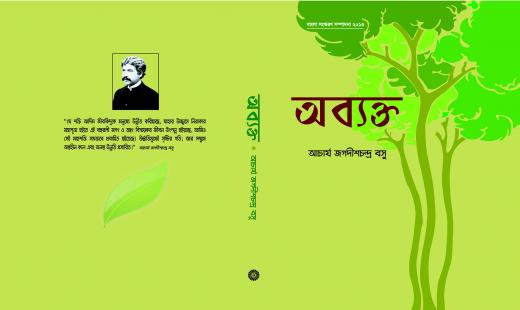 সংস্করণ সম্পাদনা ২০১৩ ভূমিকা
সংস্করণ সম্পাদনা ২০১৩ ভূমিকা
আবেগময় জীবনের সন্ধান…
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি। এ-সময় পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান জগতে কিছু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা পূর্বের ধারণাকৃত কিছু তত্ত্বকে শুধু প্রমাণই করলো না, চিন্তাভাবনায় নতুন মোড় নিল। তার একটি হলো জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ। এই সমীকরণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব। হেইনরিখ হার্টজ গবেষণাগারে শুন্যস্থান সৃষ্টি করে বিদ্যুৎচম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্বের প্রমাণ দিলেন ১৮৮৭ সালে। ১৮৯৪ সালে এই তড়িৎচম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে সঙ্কেতবার্তা প্রেরণের সম্ভাবনার কথা বললেন ভারতীয় বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ বসু। এ সম্পর্কে তিনি কলকাতা টাউন হলে বক্তৃতাও দিলেন। এর সূত্র ধরে ১৮৯৫ সালে তিনি সর্বপ্রথম একটি কঠিন দেয়ালের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গকে তারহীনভাবে ওপারে প্রেরণ প্রমাণ করেন। বিশিষ্টজনেরা এর সাক্ষীও ছিলেন। এটা ছিল বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বেতার অংশের। ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরে জগদীশচন্দ্র ইংল্যান্ডের রয়্যাল ইনস্টিটিউটের এক সভায় বেতারবার্তা প্রেরণের যে প্রমাণ-চিত্র প্রকাশ্যে দেখালেন তাতে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবুও পৃথিবী জগদীশের প্রাপ্য সম্মানটি দিতে পারেনি। সমসাময়িক এরকম আরেকটি কাজ করেছিলেন রাশিয়ার পোপভ। তিনি ১৮৯৫ সালে একই ধরনের পরীক্ষা করেছিলেন।
ভাবতে আশ্চর্য লাগে এজন্য যে, জগদীশচন্দ্র আর ও-পথে হাঁটলেনই না। হার্টজের পরীক্ষায় পাওয়া বিদ্যুৎচম্বকীয় তরঙ্গের বেতার অংশটির বিশেষত্ত্ব দেখিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে যাত্রা করলেন। যা শুধু তুলনা করা যায় আইজ্যাক আসিমভের সৃষ্টি ফাউন্ডেশন গল্পের গায়া উপলব্ধির সাথে। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করলেন প্রাণী, উদ্ভিতজগৎ এবং জড়জগতের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি তাঁর ভাবনাগুলো বলেই শেষ করলেন না, নিজের তৈরি যন্ত্রপাতি দিয়ে জীবজগৎ ও জড়জগতের মতো ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের সাড়াগুলো বোঝার চেষ্টা করলেন। এগুলোকে গভীরভাবে চিন্তা করলে মনে হয় হয় জড়-চেতনা ও জৈবিক- চেতনায় কোথায় যেন একটা সম্পর্ক আছে। বিষয়টি চারপাশের ভিন্ন ভিন্ন জগতের মধ্যে অখণ্ডতার কথা বলে; এতে বিশ্বজগতকে উপলব্ধি করা সহজ হয়। এমনসব বিষয়কে তিনি পর্যবেক্ষণে এবং বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করতে জীবনের ত্রিশ বছর কাটিয়েছিলেন।
এরই ফলস্বরূপ গ্রন্থ জড় ও জীবের সাড়া বা Response in the Living and Non-living গ্রন্থটি লেখেন। ১৯০৩ সালে লন্ডনের লংম্যান গ্রীন এ্যাণ্ড কোম্পানী থেকে প্রকাশিত হয় ওটি। ১৯২৪ সালের মধ্যে আরো ১০টি গ্রন্থ বের হয়। ‘জীব ও জড়ের সাড়া’ নিয়ে তাঁর গবেষণাসমগ্র পৃথিবীকে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করেছিল। আর এ গবেষণার বিষয়টি ‘গাছেরও যে জীবন আছে তা বাঙ্গালি বিজ্ঞানী বসুর আবিষ্কার’ শিরোনামে ব্যাপক পরিচিত পায়। গাছের প্রাণ আছে- এটা বহুকাল আগে থেকেই মানুষ জানে। না-হলে লিনিয়াস, ডারউইন, ম্যান্ডেলরা কাজ করলেন কিসের ভিত্তিতে? আসলে বসুর আবিষ্কার ছিল জড় ও জীবের সাড়া সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এটা জগদীশচন্দ্র বসুকে না-বোঝা এবং বিজ্ঞানসম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে না-ওঠার কারণেই হয়েছে।
জগদীশচন্দ্র বসুর ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থটি পড়লে জগদীশচন্দ্র বসুর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো বুঝতে অনেক সহজ হয়। অব্যক্ত গ্রন্থটা ছোট। প্রবন্ধগুলোও কিছুটা অগোছালো। কিন্তু কথাগুলো অনেক অন্তরের এবং গভীতর আত্মবিশ্বাস থেকে উঠে আসা। উঠে এসেছে বাংলার জল হাওয়া কাদা থেকে। জগদীশ’র- লেখার এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে নিয়ে যায় আর্কিমিডিসের কাছে। বিশেষত তার মেথড গ্রন্থটির (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০সালে) কথা মনে করিয়ে দেয়। আর্কিমিডিস এই গ্রন্থটিতে তাঁর আবিষ্কারগুলোর ব্যাখ্যা দেননি, দিয়েছন কী পদ্ধতিতে সেই আবিষ্কার করলেন তার। কেন তার এরকম মনে হল, কেন তাতে আগ্রহ জন্মালো। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ ধরনের রচনা একটি অসাধারণ ঘটনা। জগদীশচন্দ্র বসুর অব্যক্ত গ্রন্থটিও অনেকটা তাই। তার চিন্তাগুলোর সূচনা কিভাবে হয়েছে, সেগুলো অন্যদের কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও তিনি তা নিয়ে নিরন্তর কাজ করে গেছেন। তাঁর এই গ্রন্থটি বৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তার বিশ্বকে ধারণ করলেও ওটি পড়লেই যে কেউ বুঝতে পারবে যে, এটি বাংলার মাটির গন্ধ নিয়েই লেখা হয়েছে। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, ‘তাঁর বিজ্ঞানমন্দিরে সাফল্য দিতে হবে জগতকে, কোনোটিরই গোপনীয়তা বা প্যাটেন্ট করে রাখা চলবে না, কেননা বিজ্ঞানের সেইটিই একমাত্র ভালো যা সকলকে দেওয়া যায়, যা গোপন করতে হয়, তাই মন্দ।’
তিনি ইউক্লিড ও আর্কিমিডিসীয় ধারার মূল্যবোধ নিয়ে জীবনভর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলোকে চালিয়ে গেছেন। প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও তিনি যেভাবে তাঁর কর্মকাণ্ডগুলোকে সফলতার শীর্ষে উন্নীত করেছিলেন তা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৮ সালে ৩০ নভেম্বর বিক্রমপুরে। বসু বাঙ্গালি রেনেসাঁর অন্যতম স্রষ্টা, উপমহাদেশের প্রথম সার্থক বিজ্ঞানী। তাঁর জন্মের ঠিক তিন বছর পর জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেজন্য এ সময়কে অবিভক্ত বাংলার বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনালগ্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জগদীশচন্দ্র তাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে লিখেছেন, ‘শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাংলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজি স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলের দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাসীর পুত্র এবং বাম দিকে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর বৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবত প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে আমার অনুরাগ এইসব ঘটনা হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল।’
জগদীশ তাঁর আবিষ্কারে দেখিয়েছেন যে মানুষের বাইরেও আবেগময় জীবন আছে। কিন্তু তার বন্ধু মহাপণ্ডিত লর্ড কেলভিন স্বীকার করেননি এবং জগদীশচন্দ্রকে বলেছিলেন, ‘তা সম্ভব নয়, এটা হবে ঈশ্বর সম্পর্কে শ্রদ্ধার অভাব, ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন এক বিশেষ অধিকার।’ জীব ও জড়ের সম্পর্ক আর উত্তেজনায় প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক সাড়া বা ফলাফলগুলোকে তিনি প্রবন্ধের আকারে প্যারিসের এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে পাঠ করেছিলেন। তার সমকালীন পাশ্চাত্যের শারীরবিদদের ধারণা ছিল, কোনো বস্তুকে আঘাত করলে তা যদি বৈদ্যুতিক উপায়ে সাড়া দেয় তাহলে বুঝতে হবে, সেই বস্তুতে প্রাণ আছে। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা প্রমাণ করেছিল গাছের শরীরে বা প্রাণীর মাংসপেশীতে আঘাত করলে তা যেমন বৈদ্যুতিক উপায়ে সাড়া দেয় টিনের তারকে আঘাত করলেও (দুমড়ে-মুচড়ে দিলে) একইভাবে তা বৈদ্যুতিক উপায়ে সাড়া দেয়। তিনি তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে উপস্থিত শারীরবিদ্যার গবেষক আর বিজ্ঞানীদের কাছে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাহলে প্রাণের সংজ্ঞা কি? জীবনের সংজ্ঞা কোথায় দাঁড়াবে? তাঁর আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। যন্ত্রটির নাম দেয়া হয়েছিল ‘গ্যালেনা ডিটেকটর’। জগদীশচন্দ বসুর গবেষণাগুলোই বিধৃত আছে : Response of Inorganic and living matter গ্রন্থে (সাল)।
প্রেসিডেন্সি কলেজের ২৪ স্কয়ার ফিট আয়তনের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে তার গবেষণাগারের কাজ শুরু হয়েছিল। ঘরটি অবশ্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশেষ অনুরোধের মাধ্যমেই তিনি পেয়েছিলেন ১৯৮৮ সালের দিকে। কিছু দিনের মধ্যেই মনের মতো করে বসু তাঁর গবেষণাগারটি সাজিয়ে ফেলেছিলেন। টেকনিশিয়ান হিসেবে নিরক্ষর এক টিনের কারিগরকে হাতে-কলমে গবেষণার যন্ত্রপাতি তৈরি করা শিখিয়েছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক রোঁমা রোলাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটে ১৯২৪ সালের ২৮ মার্চ। জগদীশচন্দ্র রোলাঁকে তাঁর একটি বই ‘সারকুলেশন এন্ড আ্যসিমিলেশন অব প্লান্টস, লন্ডন, ১৯২৪’ পাঠান। সাথে একটি চিঠিও লেখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, ‘মানবতার সার্বজনীন স্বার্থের জন্য আপনার কর্মসাধনা আমার গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেগ করেছে। প্রাণের ঐক্য সম্পর্কে আমার বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার একটি কপি পাঠালাম, বিগত ত্রিশ বছর যাবৎ ভারতর্ষে এটি ছিল আমার অনুসন্ধানের বিষয়।’
তাঁর ‘প্লান্ট অটোগ্রাফ অ্যান্ড দেয়ার রিলেশনস’ বই থেকে আমরা উদ্ভিদ ও অজৈব পদার্থের সংবেদনশীলতা সম্পর্কে জানতে পারি। তার অাবিষ্কৃত নতুনজগত উদ্ভিদ ও অজৈব পদার্থের সংবেদনশীলতা ঘিরে গবেষণার সূত্রপাত ঘটে ত্রিশ বছর আগে। মূলত জানালার কাছের একটি গাছের দোলুনি দেখে তাকে দিয়ে কথা বলানোর আকাঙ্খার জন্ম নেয়, যেজন্য উদ্ভাবন করেন তিনি অনেকগুলো জটিল যন্ত্র, এগুলোর সাহায্যে গ্রাফের মাধ্যমে গাছকে দিয়ে লিখিয়ে নেন গাছের আপনকথা।
তিনি নিশ্চিত যে জীবন এক ও গতিশীল আর আমাদের অস্তিত্বের চক্র জৈব ও অজৈব পদার্থের সমরাজত্বের মধ্য দিয়ে এক রূপ থেকে অন্যরূপে আমাদেরকে নিয়ে যায়। রোলাঁকে তিনি বললেন ‘আমি যদি উদ্ভিদ না হতাম, তাঁকে বোঝার জন্য যদি আবার উদ্ভিদ না-হয়ে যেতাম, তাহলে তার মন আবিষ্কার করতে পারতাম না।’ রোলাঁ তাই বলেছিলেন, ‘এজন্যই জগদীশচন্দ্র মানবতার ঐক্যে বিশ্বাসী এবং মনে করেন শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ মানুষের মনোজগৎকে মরুভূমি বানিয়েছে’।
জগদীশচন্দ্র বসু মনে করতেন, ‘কোনো বিজ্ঞানীর অর্জন পুরো মানবজাতির অর্জন। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মুনাফাপ্রাপ্তির উৎস নয়।’ প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলতেন, ‘বিজ্ঞানের অনুশীলন কেবল বিজ্ঞানের জন্যই করিতে হবে এবং তাহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে এমন লোকের প্রয়োজন।… ইউরোপে গত শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের এমন সব সেবক জšি§য়াছেন, যাহারা কোনোরূপ আর্থিক লাভের আশা না করিয়া বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানচর্চা করিয়াছেন’।
আমি প্রায়শ ভাবি আমাদের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য কী? এটা ভেবে আমি ক্রমশ পিছন দিকে যেতে থাকি। দেখি এক স্বর্ণোজ্জ্বল সময়। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু মেঘনাথ সাহা, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রাধাগোবিন্দ। তখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসে তারা আসলে কোন দেশের, বাংলাদেশ, না ভারত তথা পশ্চিমবাংলা। আমরা বিভ্রান্ত হই। আমার বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করি। কী ভয়াবহ বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্ছিন্নতা! রাজনৈতিক ভুলের মাশুল দিতে হয় বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য রচনায়। বিজ্ঞানকে শক্তিশালী করতে এই ঐতিহ্যগুলোকে যুক্ত করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।
জগদীশের প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে লিখেছিলেন বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ ‘বিশ্ব-পরিচয়’। অর্থের অভাবে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা যখন প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়েছিল, তখন বন্ধুর গবেষণা যেন কোনোভাবে বন্ধ না হয়, সে বিষয়ে মূল উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে এ সত্যকে উপলব্ধি করে জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছিলেন ‘বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে প্রযুক্তি শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করে শিক্ষিত দেশপ্রেমিক ভদ্রলোকেরা বৃথা শক্তি অপচয় করছেন।’ এতে বোঝা যায় এ বাঙালি বিজ্ঞান মনীষীর বিজ্ঞান-প্রীতি কতোটা গভীর আর নিখুঁত ছিল। তাঁর আজীবনের কষ্টের ফসল বসু মন্দিরে লেখা আছে, ‘আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হবেন না। বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতে জ্ঞান সার্বভৌমরূপে প্রচারিত হয়েছিল। এদেশে নালন্দা তক্ষশীলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হয়েছিল।… যখনই আমাদের দেবার শক্তি জন্মিয়াছে তখনই আমরা তা মহৎরূপে দান করিয়াছি’। তিনি সাফ সাফ ঘোষণা করলেন, তাঁর গবেষণাগারের সব উদ্ভাবন ও আবিষ্কার হবে জনগণের সম্পত্তি। ওর ওপর কারো কোনো প্যাটেন্ট বা ব্যক্তিমালিকানা থাকবে না।
জনবোধ্য বিজ্ঞানের বই হিসেবেও বাংলায় লেখা ‘অব্যক্ত’ তাঁর এক অসাধারণ গ্রন্থ। যুক্তকর, আকাশ স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ, গাছের কথা, উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু, অদৃশ্য আলোক, ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে, বিজ্ঞানে সাহিত্য, নির্ব্বাক জীবন, স্নায়ুসুত্রে উত্তেজনা প্রবাহসহ অনেকগুলো প্রবন্ধ আছে। যেগুলো লিখতে শুধু যুক্তিবোধ কাজ করেনি, করেছে গভীর উপলব্ধিবোধ। তিনি বাংলাভাষায় প্রথম সায়েন্স ফিকশন লেখেন… পলাতক তুফান (১৯৩৭)। এই গল্পটি অব্যক্ত গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়। ‘অব্যক্ত’ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। বাংলা সংস্করণ সম্পাদনায়-২০১৩ বইটিকে নির্ভুলভাবে প্রকাশের বিষয়টি দেখা হয়েছে, বইটি পাঠ কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটাও বলা চেষ্টা করা হয়েছে।
আধুনিক ভাষায় বললে বইটি কসমোলজি বা বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বের ওপরই। এরকম বিষয়ভিত্তিক এবং সরল উপস্থাপনের বিজ্ঞান বইগুলোকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ডিসকাশন প্রজেক্ট একটি উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। যে বইগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে সেগুলো প্রয়োজনীয় সম্পাদনাসহ প্রকাশের ব্যবস্থা করবে। সেই সাথে নতুন বিজ্ঞানের বই লিখবে বিজ্ঞানকর্মীরা। এ ব্যাপারে প্রকাশনা সংস্থা তাম্রলিপিও এগিয়ে এসেছে স্বতস্ফূর্ত অবস্থান নিয়ে। ডিসকাশন প্রজেক্ট দীর্ঘ ২১ বছর বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে; বিজ্ঞান ভাবনা নিয়ে তরুণ প্রজন্মের সাথে বসেছে এবং গণমাধ্যমগুলোতে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এবার বিজ্ঞান বক্তৃতার পাশাপাশি প্রকাশিত বইগুলোকে নিয়ে দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে ছুটে যাবে বিজ্ঞানের বার্তা পৌঁছে দিতে। বিজ্ঞান অন্ধকারের প্রদীপ। আসুন এ প্রদীপের আলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেই। জ্ঞানই আমাদের গন্তব্য।তাম্রলিপি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ সংস্করণ সম্পাদনা
বাংলা সংস্করণ সম্পাদনা: আসিফ
প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০১৪
মূল্য: ১৬০ টাকা
পৃষ্ঠা: ১২৮
প্রচ্ছদ: যোয়েল কর্মকার
ISBN: 984-70096-0240-5






















